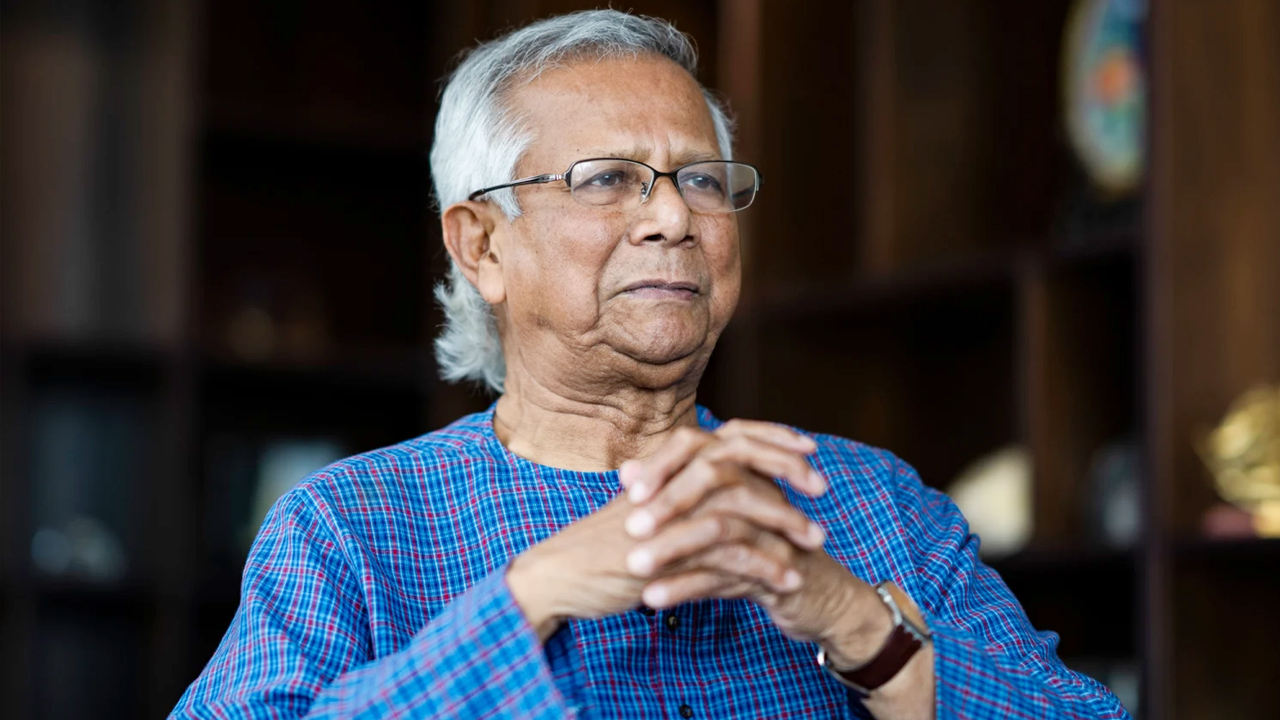প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা নববর্ষ উদযাপনের অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল হালখাতা। গ্রামগঞ্জ-নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষে পুরোনো হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় আগের জৌলুশ না থাকলেও ধুঁকে ধুঁকে এখনো টিকে আছে সেই ঐতিহ্য। বিশেষ করে পুরান ঢাকার আদি ব্যবসায়ীরা হালখাতা এখনো টিকিয়ে রেখেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও টিকে আছে কোনোরকমে।
মোগল সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেন। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে হালখাতা শুরু থেকেই নববর্ষের অপরিহার্য অংশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এখনো অল্পবিস্তর ধরে রেখেছেন হালখাতার ঐতিহ্য।
সোমবার (১৪ এপ্রিল) পহেলা বৈশাখ, বাংলা ১৪৩২ সাল শুরু। পুরান ঢাকার যে ব্যবসায়ীরা হালখাতা করেন তারা জানিয়েছেন, করোনা মহামারি ও এরপর গত দু’বছর ঈদের ছুটির মধ্যে পহেলা বৈশাখ হওয়ায় সেভাবে হালখাতা করা যায়নি। এবার কিছুটা অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে।
‘হাল’ শব্দটি সংস্কৃত এবং ফারসি– দুই ভাষায়ই রয়েছে। সংস্কৃতে ‘হাল’ অর্থ ‘লাঙল’, অন্যদিকে ফারসিতে ‘হাল’ অর্থ হচ্ছে ‘নতুন’। ঐতিহাসিকদের মতে, হালখাতার ইতিহাস কৃষিপ্রথার সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ কৃষিপ্রথার সূচনার পর হাল বা লাঙল দিয়ে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের পর সেই পণ্য বিনিময়ের হিসাব একটি বিশেষ খাতায় লিখে রাখা হতো, যেটি ‘হালখাতা’ হিসেবে পরিচিত ছিল।
‘হালখাতা’অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। ওই সময়ে ফসল বিক্রি করে হাতে সবার নগদ টাকা থাকতো। হাতে নগদ টাকা না থাকায় বাধ্য হয়েই সারা বছর বাকিতে জিনিসপত্র কিনতেন কৃষকরা। নববর্ষের সময় ফসল বিক্রি করে বকেয়া পরিশোধ করতেন। নতুন বছরে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন ব্যবসায়ীরা। সেই খাতা লাল কাপড়ে মোড়ানো। হালখাতা ঘিরে উৎসব জমে উঠতো। খাওয়াতো হতো মিষ্টি-মেঠাই।
নতুন প্রজন্মের ব্যবসায়ীরা হালখাতা নিয়ে উৎসাহী নয়। নগদ টাকা হাতে থাকায় মানুষও আর আগের মতো সেভাবে বাকির ওপর নির্ভরশীল নয়। যেটুকু বাকি পড়ে তা নির্দিষ্ট সময়ে আদায়েও আগ্রহী নন ব্যবসায়ীরা। তাই তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষ ও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার দাপটে এখন ব্যবসা-বাণিজ্যে হালখাতার ঐতিহ্য ম্রিয়মান।
টিকে আছে পুরান ঢাকায়
দেশের অনেক জেলায় হালখাতার প্রচলন থাকলেও তা আগের মতো নেই। আগে হালখাতা উপলক্ষে দোকান সাজানো হতো, খাওয়ানো হতো মিষ্টি। এসব আগের চেয়ে কমেছে। তবে স্বল্পপরিসরে হলেও টিকে আছে।
ঢাকার মধ্যে পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার, শাঁখারী বাজার, শ্যামবাজার, ইসলামপুর, চকবাজার, বাবুবাজার, বাদামতলীতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখনো নববর্ষে হালখাতার প্রচলন রয়েছে।
পুরান ঢাকার নববর্ষের ঐতিহ্য বলতে পারেন এ হালখাতা। বিশেষ করে তাঁতীবাজার, শ্যামবাজার, চকবাজার, বাদামতলী, ইসলামপুরের ব্যবসায়ীরা এখনো হালখাতা করেন। এসব জায়গায় পুরোনো ব্যবসায়ীরা এখনো নিয়ম করে নববর্ষে হালখাতা করেন।- ব্যবসায়ী মিলন ঘোষ
তাঁতি বাজারের কে বি গোল্ড হাউজের ম্যানেজার মিলন ঘোষ বলেন, ‘আগামী ১৪ ও ১৫ এপ্রিল দু’দিনই আমাদের হালখাতার অনুষ্ঠান রয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী আমরা ১৪ এপ্রিল হালখাতা করি। আর ১৫ এপ্রিল সনাতন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী হালখাতা ও পূজা দেওয়ার প্রোগ্রাম থাকে। কাস্টমাররা আসে, তাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়, উপহার দেওয়া হয়। হালখাতা উপলক্ষে দোকানে সাজসজ্জা করা হয়।’
তিনি বলেন, ‘হালখাতার দিন দেনাপাওয়া পরিশোধ হয়। ক্রেতারা নতুন করে লেনদেন করেন। সারা বছর যারা লেনদেন করেছে আমরা তাদের উপহার দেই।’
তাঁতী বাজারের ৯৫ শতাংশ দোকানে হালখাতা হয় জানিয়ে তিনি বলেন, ‘করোনাভাইরাস মহামারির পর থেকে হালখাতায় সাড়া মেলেনি। গত দু’বছর তো ঈদ আর নববর্ষের ছুটি একসঙ্গে থাকায় নববর্ষ সেভাবে হয়নি। এবার একটু গ্যাপ দিয়ে নববর্ষ হচ্ছে, আশা করছি হালখাতাও ভালো হবে, ক্রেতাদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাবে।’
‘পুরান ঢাকার নববর্ষের ঐতিহ্য বলতে পারেন এ হালখাতা। বিশেষ করে তাঁতীবাজার, শ্যামবাজার, চকবাজার, বাদামতলী, ইসলামপুরের ব্যবসায়ীরা এখনো হালখাতা করেন। এসব জায়গায় পুরোনো ব্যবসায়ীরা এখনো নিয়ম করে নববর্ষে হালখাতা করেন।’ বলেন মিলন ঘোষ।
শ্যামবাজারের বনলতা বাণিজ্যালয়ের মালিক ওবায়দুল ইসলাম মানিক বলেন, ‘শ্যামবাজারের ব্যবসায়ীরা এখনো হালখাতা করেন। তবে এখন আর একটি নির্দিষ্ট দিনে সবাই একসঙ্গে করেন না। কারণ একজন পাইকার বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেন করেন। সবাই একদিনে হালখাতা করলে তো একই কাস্টমার তিন-চারজনের বাকি একসঙ্গে দিতে পারবে না। তাই আলাদা আলাদাভাবে করলে কাস্টমারের সুবিধা হয়। এজন্য কেউ নববর্ষের আগে, কেউ নববর্ষের দিন বা কেউ নববর্ষের পরে হালখাতা করেন।’
তিনি বলেন, ‘আমরা হালখাতা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি। কয়েকজন নববর্ষের দিন করবেন, চিঠিও পেয়েছি। ঈদের পর থেকেই এখানে হালখাতা শুরু হয়ে গেছে।’
ওবায়দুল ইসলাম আরও বলেন, ‘হালখাতার দিন গ্রাহকরা দু-তিন বছরের বকেয়া টাকাটা আমাদের দেন। আমরা তাদের জন্য মিষ্টি, বিরিয়ানি দিয়ে ভোজনের আয়োজন করি। কেউ পুরো বকেয়াটা পরিশোধ করে, কেউ কিছু পরিশোধ করে। যা বাকি থাকে সেটা নতুন খাতায় ওঠানো হয়, নতুন বছরে এ খাতা চলে। পুরোনো খাতা বাদ।’
হালখাতা শুরুর ইতিহাস
বাংলা সনের সূচনার ইতিহাস ঘিরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠিত মত হলো- ১৫৫৬ সালের ৫ নভেম্বর যখন মোগল সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসেন তখন থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। মোগল আমলে হিজরি সাল ব্যবহার করতেন রাজস্ব আদায়ের কাজে। কিন্তু হিজরি সাল ব্যবহারের কারণে কৃষকদের সমস্যা হতো। কারণ চন্দ্র ও সৌর বছরের মধ্যে ১১ বা ১২ দিনের পার্থক্য ছিল। ফলে ৩১টি চন্দ্র বছর ৩০টি সৌর বছরের সমান হয়ে যেত। রাজস্ব চন্দ্র বছর অনুযায়ী আদায় করা হতো, আর চাষাবাদ করা হতো সৌরবছর অনুযায়ী। এতে অসময়ে কৃষকদের খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হতো।
খাজনা আদায়ের এ সমস্যা অনুধাবন করে সম্রাট আকবর একটি বৈজ্ঞানিক কিন্তু কার্যকর সমাধান খুঁজছিলেন। তাই তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্বিদ আমির ফাতুল্লাহ শিরাজীকে পরিবর্তন আনার আদেশ দেন। ১৫৮৪ সালে সম্রাট আকবর সরকারিভাবে চালু করেন বাংলা ক্যালেন্ডার, যা বাংলা সাল নামে পরিচিত। এটা প্রথমে তারিখ-এ-এলাহি নামে পরিচিত ছিল এবং ১৫৮৪ সালের ১১ মার্চ এই প্রথা চালু করা হয়। এটা আকবরের রাজত্বের ২৯ বছরে চালু করা হলেও তা গণনা করা হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনে বসার বছর ১৫৫৬ সাল থেকে। এটি কৃষকদের কাছে ‘ফসলি সন’ নামে পরিচিত ছিল, যা পরবর্তীসময়ে ‘বাংলা সন’ বা ‘বঙ্গাব্দ’ নামে পরিচিতি পায়। সেই সময় থেকেই ব্যবসার হিসাব করার জন্য হালখাতার প্রথা চালু হয়।
বাংলা সাল চালুর ধারাবাহিকতায় চৈত্র মাসের শেষ দিন চৈত্র সংক্রান্তিতে জমিদারের প্রতিনিধিরা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন এবং পরবর্তী বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখে জমিদাররা প্রজাদের মিষ্টি, মিষ্টান্ন, পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। নববর্ষের হালখাতায় পুরোনো বছরের খাজনা আদায়ের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খোলা হতো। একসময় বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ একটি নতুন রীতি প্রচলন করেন, যেটি একসময় ‘পুণ্যাহ’ হিসেবে পরিচিত ছিল।
‘পুণ্যাহ’র বিষয়ে ড. এম এ রহিমের ‘বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত)’ বইতে রয়েছে, ‘নবাব কর্তৃক উৎসবসমূহ বিরাট ঐশ্বর্য আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হতো এবং এসব উৎসবের আমোদ-প্রমোদে জনসাধারণ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতো। বিরাট আনন্দ, উৎসব ও আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে নবাবের নওরোজ উৎসব প্রতিপালিত হতো। আর একটি উৎসব ছিল ‘পুণ্যা’। বছরের প্রারম্ভে বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের শুভারম্ভের নাম ‘পুণ্যা’। হিন্দু পঞ্জিকার ভিত্তিতে ‘চৈত’ মাসে অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে এই তারিখ নির্দিষ্ট হতো। এই দিনে বিগত বছরের বকেয়া খাজনার আদায়কৃত নগদ ছয় সাত লক্ষ টাকা থলিতে থলিতে আনয়ন করে, নবাবের সম্মুখে রাখা হতো।’
এ বইয়ে আরও বলা হয়, যদি আমিল (ফৌজদারের পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা) ও জমিদারদের দেওয়া রাজস্বের কিছু অংশ অনাদায় থাকতো তাহলে দেশের প্রধান ব্যাংকার জগৎশেঠ তাদের পক্ষে নবাব সরকারে তাদের বাকি রাজস্ব পরিশোধ করবেন, এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতেন। সব বড় বড় জমিদার, অনেক পদস্থ কর্মচারী এবং কেরানি- এরূপ চার শতাধিক ব্যক্তি তাদের পদমর্যাদা অনুসারে ‘খিলাত’ লাভ করতেন। এ উপলক্ষে নবাব দরবারে স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণখচিত কাপড়ের চন্দ্রাতপের নিচে কারুকার্যপূর্ণ বালিশ দিয়া সজ্জিত মসনদে উপবেশন করতেন এবং তার সম্মুখে রাখা হতো রাজস্ব হিসাব-নিকাশের স্বর্ণখচিত খাতা। বিরাট আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হতো।’
ব্রিটিশ আমলে ঢাকায় মিটফোর্ডের নলগোলার ভাওয়াল রাজার কাচারিবাড়ি, ফরাশগঞ্জের রূপলাল হাউস, পাটুয়াটুলীর সামনে প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান হতো। নবাবি আমল শেষে বিলুপ্ত হয় পুণ্যাহ। কিন্তু নিভু নিভু হলেও এখনো রয়ে গেছে হালখাতা।
যা হতো হালখাতায়
‘হালখাতা’ উপলক্ষে ব্যবসায়ীরা ঝালর কাটা রঙিন কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ‘শুভ নববর্ষ, শুভ হালখাতা’ লেখা থাকতো। কিছু কিছু দোকানে ধূপধুনা জ্বালানো হতো। এসময় গ্রাহক-খরিদ্দারদের মিষ্টিমুখ করানো হতো এবং হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব চলতো। পাশাপাশি চলতো বকেয়া আদায়। এছাড়াও আগত অতিথিদের জন্য পান-সুপারি এবং উপহারের বন্দোবস্ত থাকতো। আমন্ত্রণপত্র দিয়ে হালখাতার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নববর্ষের সকালে দোকানে দোকানে লক্ষ্মী-গণেশের পূজা করতেন। পূজায় সামনে রাখা হয় স্বস্তিক চিহ্নখচিত হালখাতা।
সনাতন ধর্মে স্বস্তিক চিহ্ন বিশেষ মঙ্গলবার্তা বহন করে। তাই যে কোনো পূজা বা শুভ অনুষ্ঠানে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো। ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পায়ে ঠেকিয়ে নতুন বছরের হিসাবের খাতা খোলা হতো। কখনো কখনো পহেলা বৈশাখে নতুন খাতাটি নিয়ে মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে আসতেন। পূজারিরা সিঁদুরের মধ্যে কাঁচা পয়সা ডুবিয়ে সেই পয়সা সিলমোহরের মতো ব্যবহার করে নতুন খাতায় ছাপ মেরে তা উদ্বোধন করতেন। পাশাপাশি দিয়ে দিতেন চন্দনের ফোঁটা। পয়সাকে লক্ষ্মী হিসেবে বিবেচনা করে ব্যবসায় লাভবান হওয়ার আশায় এই আচার পালন করতেন তারা।